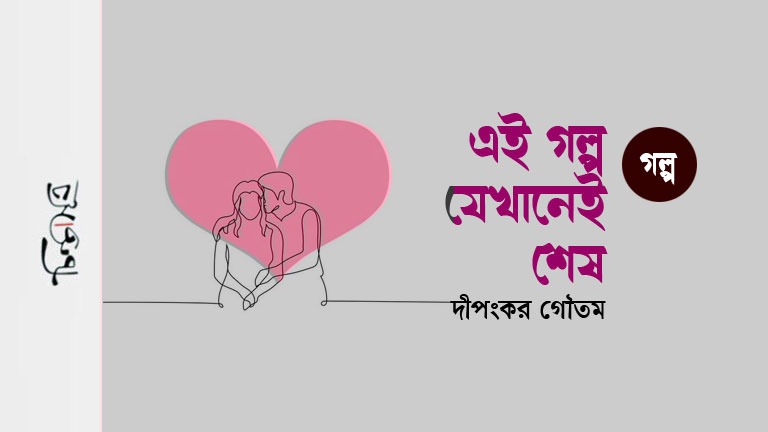জমিদার বাড়ির বিশাল ভবন থেকে এখন সোঁদা গন্ধ ভেসে আসে। ঝরে পড়ে ইট-সুরকির পলেস্তারা। কখনো পুরনো টালি পড়লে যে শব্দ হয়, তাকে ভূতের আছর ভেবে অনেকেই ভুল করে। জীর্ণ একটি ভবন আর মান-সম্মানের ছিটেফোঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জমিদারি শাসনের ক্ষত। শাসনের দিন শেষ হলেও তার যতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে , সেটাও জমিদারি শাসনের চেয়ে আলাদা কিছু নয়। জমিদার বাড়িকে ঘিরে পূর্বপুরুষদের মতো এলাকার বয়স্ক লোকেরা এখনো অনেক সম্মান করে বাড়িটিকে। স্থানীয়রা এখনো শ্রদ্ধা করে বাড়ির কর্তাকে। বিপদে-আপদে তার কাছেই আসে সবাই।
সুধারাম ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর তার সন্তান হরিরাম ভট্টাচার্য হয়ে উঠেছিলেন তাদের রক্ষাকর্তা। বিপদাপদের মহান আশ্রয়। যশোরাজ বিশ্বাস শিল্পী হওয়ার জন্য তার ওপর হরিরাম ভট্টাচার্যের ছিল বিশেষ ভালোবাসা। দিন যায় ক্ষণ যায়, এরমধ্যেই একদিন কী এক অঘটনের খবর ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। হরিরাম ভট্টচার্যের মেয়ে সুখী যশোরাজ বিশ্বাসের ছেলে সুকান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। মানুষজন ফিসফিসিয়ে এই অনাচারের গল্প করে। সুকান্ত—নমশুদ্রের ছেলে, মেধাবীও। বাঁশী বাজায়। এলাকায় অনেক সুখ্যাতি তার ভালো ছেলে হিসেবে। কিন্তু সবাই যেন স্তব্ধ হয়ে যায় ঘটনা শুনে। জমিদার ব্রাহ্মণের পরিবারের সঙ্গে এ অঘটন যেন বড় কোনো দুর্বিপাকের ইশারা দেয়। যশোরাজ বিশ্বাস ভেবেছিল সুকান্তকে কীর্তনের দলে ভেড়াবে। অভাবের সংসারে পড়াশোনার চেয়ে বাঁশি বাজালে দলের বংশীবাদকের টাকাটা বেঁচে যাবে। কিন্তু কর্তাবাবু হরিরাম ভট্টাচার্য বললেন, ‘ছেলেটি যেহেতু ছাত্র ভালো, ওকে পড়াও যশরাজ। তোমার বাড়ির পাশের জমিখানায় যে ফসল হয়, তা বেচলে সুকান্তের পড়াশোনার খরচ হয়ে যাবে। তারপর আমি তো এখনো আছি।’
যশোরাজ তাতে খুশি হয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সুখী ও সুকান্তের মধ্যে যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠলো তাতে সুকান্তকে বিয়ে করার মধ্যেই সুখী যেন জীবনের সব সুখকে আবিষ্কার করেছিল। আত্মীয়-স্বজনের মেয়েদের বিয়েতে কত টাকা খরচ হয়, সেদিকে না তাকিয়ে সুখী তার সিদ্ধান্তে অটল ছিল। সুকান্তের সঙ্গে বিয়ে করার পরেই সুখীর জীবনে শান্তির কপোত ধরা দেবে, এই আশায় বুক বেঁধে চলছিল তাদের বৈবাহিক জীবন। আত্মীয়-স্বজন প্রথম দিকেই সামান্য এক জেলের ছেলের কাছে পড়ার ব্যাপারে দ্বিমত করেছিল। সে-সব তখন কানে লাগাননি হরিরাম ভট্টাচার্য। তার প্রিয় যশোরাজের ছেলে এমন কাজ করবে, সেটা তার ভাবনায় ছিল না। কিন্তু যা ঘটার তাই ঘটলো। একদিন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার হরিরাম ভট্টাচার্যের সাজানো সংসার ও বিখ্যাত বনেদি ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারের মায়া-মমতার বাঁধন ছিন্ন করে সে সুখের আশায় চলে এসেছিল শিক্ষক সুকান্তের হাত ধরে। কার্তিকের এক জোছনাপ্লাবিত রাতে ঘর ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয় সুখী ও সুকান্ত।
সে রাতে পূর্ণিমা ছিল। ক্ষয়িষ্ণু এক জমিদার বাড়ির সুরকি ওঠা দালান বাড়ি ছেড়ে পূর্বের কথামতো সুখী যখন দিঘির পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখনো তাদের বাড়িতে কোজাগরী পূর্ণিমার লক্ষ্মীপূজার বাদ্য বাজছিল। অনেক আত্মীয়-স্বজনের মাঝ থেকে শান বাঁধানো ঘাটে এসে সুকান্ত বিশ্বাসের বাঁশীর মোহনীয় সুর শুনতে শুনতে তার পেছনে এসে দাঁড়াতেই দেখল- ধূ ধু করছে সোনামুখী বিল। সব জোছনা যেন চুয়ে পড়ছে মাঠটাতে। জোছনার সাগর মনে হচ্ছে তার চোখের গহীনে। দুধের সরের মতো কুয়াশার প্লাবনে যেন বিল ভেসে যাচ্ছে । নীলাভ ঢেউ তরঙ্গ তুলে সেখানে দোল খায়, বাঁক নেয়। সুকান্ত ভাবতেই পারেনি এত বাধা, বিত্তের বৈভব ছেড়ে, ভট্টাচার্য বাড়ির মায়া-মমতা ছেড়ে সুখী চলে আসবে। ভাবতে ভাবতেই তারা নিরুদ্দেশের পথে হাঁটতে থাকে। প্রথমে সুকান্তের একচালা ঘরের বাড়িটিতে সিঁদুর পরানোর কাজ শেষ করে সুকান্তের বাবা-মাকে প্রণাম করতে গেলেই বিপত্তি ঘটে। ব্রাহ্মণের কন্যা—যার বাবার বংশের তারা প্রজা। এখনো জুতা পরে তাদের বাড়ির পথ মাড়ায় না তারা, তাদের দান করা জায়গায় বাস করে। সেই জমিদারদের মেয়ে তাদের বাড়ির বউ হবে, এটা তারা কেউ ভাবতেই পারছিল না।
জমিদাররা তাদের আটচালার শিল্পী-বাদকদের থাকার জায়গাটা নিশ্চিত করতেন। সেভাবেই জমিদার ভট্টাচার্যদের কীর্তন গান গাওয়ার সূত্রে বাড়িখানা তারা পেয়েছিল আশ্রয় হিসেবে। জমিদারি চলে যাওয়ার পরেও সুকান্তের বাবা যশরাজ কীর্তনীয়া কীর্তনের মৌসুমে দূর দুরান্তে গান গাইতে গেলেও সুধারাম ভট্টাচার্যের পরিত্যক্ত প্রায় আটচালার মণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে সুখীর বাবা হরিরাম ভট্টাচার্যের বাড়ির সবাইকে প্রণাম করে মৌসুমে যেতো। সেই বাড়ির ছেলে জমিদার বাড়ির কন্যাকে বিয়ে করবে—এটা কেউ মেনে নিতে পারছিল না। তাছাড়া হরিরাম ভট্টাচার্যের মান-সম্মান বাঁচানোর দায়িত্ব তাদের। এমন ভাবনা নিয়েই তারা বেঁকে বসলেও একবার যে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে এসেছে তাকে ফেরাবে কী করে?
রাত পার হয়ে সকাল হলে পরিস্থিতি কী হবে—সেই ভাবনায় সবাই শঙ্কিত হলেও সিঁদুরপরানো বউ ঘরে রাখবে কিভাবে? শঙ্কায় সমস্ত বাড়ির লোক তটস্থ থাকে, তথাপি সুকান্ত সুখীর হাত ধরে রাতের আঁধারে পায়ে হাঁটা পথে নিরুদ্দেশ যাত্রায় পা বাড়ায়।
যশরাজ ও রসরাজ বিশ্বাসের পরিবার ছিল যৌথ। কারণ রসরাজ ছিলেন নিঃসন্তান। সে কারণে স্ত্রী বিয়োগের পর থেকে সে বস্তুগত লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে উঠে শুধু গানই গাইতেন। কীর্তনীয়া হিসেবে তাদের দুই ভাইয়ের প্রচুর খ্যাতি ও পরিচিতি এলাকায় না শুধু, এলাকার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের পরিবারে একমাত্র শিক্ষিত সন্তান সুকান্ত বিশ্বাস দেখতে দেখতে বিএ পাস করেছিল। বাবা-মা’র সংসারে দুটি ছেলে সন্তান নিয়ে চলছিল তাদের সুখের দিনাতিপাত। তাদের ঘরে সুকান্ত সবার বড়। ছোট ছেলে নলিনী বিশ্বাসও পড়াশোনায় এগিয়ে যাচ্ছিল। মেট্রিক পাস করার পরে সে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। বিএ পাস করলেই উঠে যাবে পরিবারটি, এমনই ধারণা ছিল সবার। তার পড়াশোনার খরচবাবদ বেশিরভাগ সাহায্য আসতো ভট্টাচার্য পরিবার থেকে। হরিরাম ভট্টাচার্য অনেক সংকটের মধ্যেও জমি-জিরাত নিম্নবর্গের মানুষদের দিয়ে চাষ করিয়ে নিতেন।
সোনামুখী বিল ছিল তার উপার্জনের উৎস। বড় কোনো পূজা-পার্বণ পড়ে গেলে জমি এখনো গোপনে বন্ধক রেখে কাজ চালাতেন তিনি। এসব কথা খুবই গোপনে করলেও সবার জানা। এক এক প্রজার কাছে জমি দেওয়ার কথা বলে টাকা এনে, ধান বিক্রি করে চলতো এই ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের জীবন-যাপন। তবু কাউকে টের পেতে দিতেন না তিনি কোনো মূল্যেই। ইতোমধ্যে অনেক প্রজা জমির মালিক বনে গেছে, তবু হরিরাম ভট্টাচার্যের দিকে তাকিয়ে কেউ কথা বলে না।
ইতোমধ্যে অর্থনীতি বদলেছে অনেকের। জেলে পাড়ার আঁশটে গন্ধ কালের স্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে। তবু সবার কাছে হরিরাম ভট্টাচার্য দেবতুল্য। তার মেয়ে বিশ্বাস বাড়ির বউ হয়ে আসবে—এটা কারও স্বপ্নেও আসে না।
চারদিকে লোকজন খোঁজাখুজি করার পরে জানা যায় তাদের দুজনকে অনেকেই সোনামুখী বিলের পথ ধরে দ্রুত হেঁটে যেতে দেখেছে। হরিরাম ভট্টাচার্য তার স্ত্রী কানন বালাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, সুখী কোথায় যেতে পারে? আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি খুঁজতেও তার ভয়। ভয়টা পুরোই মান-সম্মানের। সকাল হতেই এ খবর কিভাবে জানাজানি হয়ে যায়। কারও মুখে কোনো শব্দ সরে না। খোঁজ চলে, তাও গোপনে। দুই দিন পরেও সুকান্ত আর সুখীকে কোথাও পাওয়া না যাওয়ায় সবাই ভেবেই নেয় তারা সুখের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে। এখন কী হবে?
হরিরাম ভট্টাচার্যের অভিভাবক তার ভায়রাভাই প্রসাদ চক্রবর্তী। এলাকায় তার সততার সুখ্যাতি রয়েছে। পেশায় শিক্ষক হওয়ার কারণে সবাই তাকে সমীহ করে। দেশ গ্রামের শালিসী বিচার তার বৈঠক ঘরে হয় বলে তার কারণে ওই অঞ্চলের কাউকে থানা-আদালত করতে হয় না। বিত্ত-বৈভব তার না থাকলেও তার কথার বাইরে কেউ যায় না। তার সর্বজনীন চরিত্র, জাত-পাতের ঊর্ধ্বে তার অবস্থান হরিরাম কখনোই আমলে নিতেন না। কিন্তু মেয়ের এই জাতবিরোধী কাজ-সর্বোপরি সমাজের তথাকথিত অস্পৃশ্য একজনের হাত ধরে চলে গেছে তার সন্তান, একথা তিনি কাকে বলবেন? নিরুপায় হরিরাম তার দ্বারস্থ হলে তিনি লোকজন না ডেকে হরিরামকে চুপ থাকার পরামর্শ দিলেও সে কথায় তার মন মানলো না। একথা চারদিকে জানাজানি হলে জেলে সম্প্রদায় এবার জোট বাঁধলো।
পরবর্তী সময়ে তিনি নিরুপায় হয়ে মান-সম্মান বাঁচানোর জন্যে দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। হরিরাম ভট্টাচার্যের ছেলেরা কলকাতায় যে যার মতো ততদিনে জায়গা করে নিয়েছে। ফলে তিনি তার অংশীদার ও চির শত্রু কাকাত ভাই শচীন ভট্টাচার্যের সঙ্গে জায়গা ভাগাভাগি করে ফেললেন দ্রুত। শচীন ভট্টাচার্যের সঙ্গে তার কোনো হৃদ্য সম্পর্ক ছিল না। এ সংকট বহু পুরানো। সুধারাম ভটাচার্য ও সীতারাম ভট্টাচার্যের ভেতরে দ্বন্দ্ব ছিল বহু পুরনো। জমিদারি কেনার সময় সীতারামকে সে জমিদারির অংশে রাখেনি। শুধু একসঙ্গে থাকার সুবাদে জমিদারি সম্পত্তির বাইরে যে জমিজমা ছিল, তারই অংশীদার হয়েছিল দুজন। সীতারামের ওপরে হরিরামের দ্বন্দ্ব প্রকট আকার নিয়েছিল সুধারামের মৃত্যুর পরে। সুধারাম মৃত্যুর আগে জ্বরে পড়েছিলেন। ডা. হিসেবে তখন জেলা সদর থেকে আনা হয়েছিল মহেন্দ্র চক্রবর্তীকে। তিনি যে ইনজেকশন লিখে দিয়েছিলেন সীতারাম সে ইনজেকশন এনে পুশ করার পরে জমিদার সুধারাম আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। হরিরাম ভট্টাচার্যসহ সবার ধারণা ছিল—জমিদারিতে অংশ না দেওয়ার কারণে সীতারাম এ কাজটি ঠাণ্ডা মাথায় করেছিলেন। ফলে সে শত্রুতা কোনোকালেই যায়নি। হরিরাম জমিদারি চালালেও তার খুড়তুতো ভাই শচীন ভট্টাচার্যের সঙ্গে মুখ দেখা-দেখিতো ছিলই না, বরং প্রায়ই গোলমাল লেগে থাকতো। যাই হোক দেশ ছাড়ার আগে দ্রুত লোক ঠিক করে তিনি তার বাসভবনও বেচে দিলেন। পুরনো ভবন যারা কিনেছিল তারা ভবন ভাঙলো, সেই ভাঙনের শব্দ সুখীর কান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছালেও ততদিনে সে বিশ্বাস বাড়ির বউ হয়ে গিয়েছে। তারপর এক ভোরে কাউকে না বলে কলকাতার উদ্দেশে পাড়ি জমালেও ভিতরে যে ঘটনাটা ঘটলো, তাহলো, গ্রামের সবাই জানলো মেয়ে হারিয়ে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার হরিরাম দেশ ছাড়া মানুষদের খাতায় নাম লেখালেন।
বাড়িতে শচীন ভট্টাচার্য থাকলেও ওই জমিদারিতে তার তেমন কোনো অংশ না থাকায় তিনি যতটুকু জায়গা পেয়েছিলেন তাতেই ভিটায় প্রদীপ জ্বললেও তার আলোর ছাপ এলাকায় পড়লো না। কিন্তু সংকট হলো সুকান্তের পরিবার। তারা তাদের কর্তাবাবুর দেশছাড়াকে এক ধরনের অভিসম্পাত বলে ধরে নিলো। বাবু দেশ ছেড়েছেন শুনে যাদের মন খারাপ হলো তাদের তালিকায় সুকান্তের বাবা-মা’ই প্রধান। এরমধ্যে ঘটলো আরেক ঘটনা। সুকান্তের একমাত্র ভাই কলেজ থেকে বাড়ি আসার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালো। নলিনী প্রাণ হারানোতে সুকান্তের বাবা-ময়ের ধারণা হলো কর্তার অভিশাপে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। সুকান্তের বাবা-মা,পাড়া পড়শীর কান্নাকাটিতে এলাকায় যে শোক নামল এলাকায় তার চেয়ে বড় ধাক্কা আছড়ে পড়ল সুখী-সুকান্তের সুখের ঘরে। এখন তাকে তিন বেলা একথাই শুনতে হলো যে তার কারণেই এ পরিবারে আগুন লেগেছে। যশোরাজ কীর্তনীয়া খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল সন্তান স্বদেশের মৃত্যুতে। তার এই অসুস্থতার মধ্যে কোনো গান তিনি আর গাইবেন না—একথা তিনি ঘোষণা করলেন। তাহলে এই পরিবারটির আর্থিক জোগান মিলবে কিসে?
তাছাড়া ফসলের ক্ষেত দেখতো ছোট ছেলে নলিনী- জমিদারের অভিশাপ সব অঘটনের মূল কারণ হিসাবে তারা দেখল। এখন সুখীর আর কোনো পথ থাকলো না। বাড়িতে কান্নাকাটি, হরিরামের আত্মীয়-স্বজনেরা যশোরাজের বাড়ির পথ বন্ধ করে দিলো। সুখীর সুখ উধাও হলো, কোন পথে শান্তির দেখা পাবে, তা আর সে বুঝে উঠতে পারলো না। হরিরামের দেশত্যাগের খবর জেলে পাড়ার যারাই শুনলেন, তারা অনেকেই শোকে মুষড়ে পড়লেন। সবার চিন্তা একটাই—এখন বিপদে আপদে তাদের সাহায্য করবে কে? বিভিন্ন পালাপার্বণে দুই/তিন দিন ভালো-মন্দ খাবার তাও হবে না, এ ছাড়াও সারাদিনে শ্রম খাটার পরে যারা আটচালায় বৈঠকী গানের আসর বসিয়ে উৎসব-উদ্দীপনায় মেতে থাকতো, তাদের আর ছায়া দেয়ার মতো কেউ রইলো না। তাছাড়া অনেকেই যারা অল্প-স্বল্প টাকা জোগাড় করে জমিতে অধিকার নিয়েছিল তারা আর জমির কাছে যেতে পারলো না। যারা বড় বড় জোতদার হয়ে উঠেছিল ইতোমধ্যে তারা জমির কাগজপত্র দেখিয়ে জমির অধিকার নিয়ে নিলো। এখন কী হবে? তাদের কষ্টে-শ্রমে দেওয়া টাকা যেন জলেই গেলো। সুখীর বাবা-মা দেশান্তরিত হলো, আত্মীয়-স্বজনের ভেতরেও বর্ণপ্রথার কারণে কারও সঙ্গে যোগাযোগের পথ আর রইলো না। এমন যোগাযোগ ছাড়া বাঁচা যায়? অন্যদিকে হরিরাম সব হারিয়ে এক মেয়ের জন্য এলাকাবাসীর সব শ্রদ্ধা সম্মানকে পিছু ফেলে যে কলকাতায় গেলেন সেখানেও তার ভাগ্য বিড়ম্বিত হলো। কলকাতার আত্মীয়-স্বজন-সন্তান যারা ছিল তাদের মধ্যেও তার প্রতি অসম্মানের মনোভাব তাকে আশাহত করলো।
বার্ধ্যক্য এসে পড়ায় হরিরাম ভট্টাচার্যের কোনো কাজ করার ক্ষমতাও তখন আর নেই। অতপর পুরনো এক বংশধর জটিলেশ্বরের বাড়িতে তার আশ্রয় জুটলেও অকৃতদার জটিলেশ্বরের বাড়িতে তার স্ত্রী কাননবালা রান্না-বান্না করে স্বামীকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলেও রোগে শোকে ক্রমশ দুজনেই প্রায় অচল অবস্থায় পড়লেন। অল্পকাল পরেই একদিন এলাকায় তাদের মৃত্যুসংবাদ এলো। এসব খবর যখন সুখীর কানে গেলো সুখী যেন আর কষ্টের ভার সইতে পারলো না। সুখীর সুখের জন্য একটি পরিবার শেষ হয়ে গেলো। এই দায় নিয়েই সে স্বামীর সঙ্গে স্কুলে চাকরি নিলেও চাকরি শেষে এসে সংসারের নানান কাজে তাকে হাত দিতে হতো। মৌসুমি ফসলের কাজ করতে করতে সে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। বাবা-মায়ের মৃত্যুশোক তাকে কাহিল করে তুললো। কলকাতা থাকা অবধি কোনো কাজের সঙ্গেই সে আর সম্পৃক্ত থাকতে পারলো না। অন্যদিকে তিনবেলা শাশুড়ির অভিসম্পাতে তার জীবন আর জীবন থাকলো না শেষমেষ। এর মধ্যে পরপর দুটি সন্তান হওয়ায় সুখী যেন তাদের লালন-পালন করে কুলিয়ে উঠতে পারছিল না। পাড়া-পড়শী কেউ তার আপন হলো না। ফলে স্কুলের সহকর্মীদের কাছে কান্নাকাটি করা ছাড়া তার আর সব পথ যেন বন্ধ হয়ে রইলো। এভাবে দিনের পর দিন পার করতে করতে তার সন্তানরাও বড় হয়ে উঠতে থাকলো। আর সেই সন্তানেরা মায়ের কষ্ট বোঝার কোনো পর্যায়ে থাকেনি। অন্যদিকে কোলকাতার ভাইদের দরিদ্র পরিবার তার মুখাপেক্ষি হয়েও কাউকে পরিচয় দিতো না। কিন্তু সবদিক সামলাতে তার স্কুলের বাইরেও টিউশনি করতে করতে রাত অনেক হতো। সেসব নিয়েও পরিবারে অশান্তি তীব্র হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে সুকান্ত মানুষটিও যেন তার অপরিচিত হয়ে উঠলো। এই গৃহদাহ নিয়ে বহু দেনদরবারের মধ্যে তার শাশুড়ির ব্রেইন স্ট্রোক তাকে আরও সংকটে ফেলে দিলো। এক সংস্কৃতি থেকে আরেক সংস্কৃতিতে সে ক্রমশ বেমানান হয়ে উঠলো। তার বাড়ির কাকা শচীন ভট্টাচার্য বিভিন্ন পার্বণ ধরে রাখলেও সে-সব উৎসবের বাদ্য তার কানে যখন আছড়ে পড়তো তখন লুকিয়ে কান্না ছাড়া আর কিছুই তার করার রইলো না। তার ভেতরে যেমন জমিদার পরিবারের সংস্কৃতি ধিকিধিকি করে বেঁচে রইলো, সুকান্তের ভেতরেও তেমনটিই হলো। ফলে বর্ণপ্রথার পাঁচিল ডিঙিয়ে মানুষ হওয়ার বিষয়টি ক্রমশ মেঘের ভেতরে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল। যশোরাজের মৃত্যু, তার শাশুড়ির স্ট্রোক সব কিছুর জন্য দায়ী হলো সুখী। এই দায় ও পরিবারের সবার অভিসম্পাত প্রতিক্ষণে স্বপ্নে সাজানো বাগান যেন বিরান ভূমিতে পরিণত করলো।
অতপর একদিন মধ্যরাতে একগাছা দড়ি হাতে সে ঘুমন্ত বাড়ি ছেড়ে শান্তির আশায় সোনামুখী বিলের ভেতর দিয়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলো। তখন বিলের চারদিকে সমস্ত পাড়া ঘুমিয়ে পড়েছে। অশোক বনের ডালে নতুন ফুল এসেছে। কুয়াশার হালকা পাতলুন চিরে সে হাঁটতে শুরু করলো মুক্তির পথে। যে করেই হোক—এ জীবন রাখার স্বপ্ন তার আর রইলো না। এই সোনামুখী বিল তার ঠাকুরদাদার তালুক ছিল, ধান ছিল, গান ছিল—ঢাকের বাদ্যে মুখরিত হতো বস্তুপাড়া। এখন সেসবই স্মৃতি। সেই স্মৃতির পসরার আলভাঙা পথ দিয়ে তার মধ্যেই সে দ্রুত পায়ে হেঁটে চললো—মুক্তির আশায় কোনো এক সুখের দেশে। নিশুতি রাতের বাঁশির বেহাগ, বৈঠকি গানের সুর আর তাকে ধরে রাখতে পারলো না। অন্যদিকে ঘুমের ঘোরে সুখীকে ঘরে না পেয়ে সুকান্ত তাকে খুঁজতে বের হলো—অন্ধকার তখন যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। সুকান্ত সুখী সুখী ডাকতে ডাকতে পিছু হাঁটতে থাকায় দূর থেকে ছায়ার মতো কিছু একটা দেখা গেলেও সুখী কোনো ডাকেই আর ফিরলো না। জাত-পাতের বেড়াজাল এক্ষেত্রেও মস্তিষ্কে পাঁচিল টপকাতে ব্যর্থ হলো। এই গল্প যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে বেত্রবতী নদীর জলে পাখিরা চঞ্চু ধুয়ে ভোরের ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছিল। সুকান্ত-সুখী জোর পায়ে তখনো হেঁটে চলছিল।